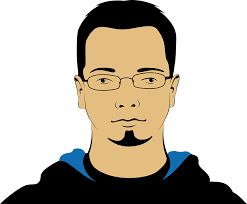

অলিউল্লাহ নোমান এর টাইমলাইন থেকে :
শেখ মুজিবুর রহমান আড়াই বছরে সংবিধানে চারটি সংশোধনী এনেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর অনুমোদিত হয় দেশের প্রথম সংবিধান। তবে এটাও সত্য, সংবিধান অনুমোদন করেছিল পাকিস্তানের জন্য গঠিত গণপরিষদ। পাকিস্তানের সংবিধান রচনা এবং পাকিস্তান শাসনের জন্য ১৯৭০ সালে মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। সেই গণপরিষদই স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেছিল। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত ছিলেন না।
সংবিধান চুড়ান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে। এ সংসদ সংবিধানে ৪টি সংশোধনী আনে। এর মাঝে চতুর্থ সংশোধনী আলোচিত এবং সমালোচিত।
চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের মলাটের অভ্যন্তরে সব পাল্টে দেয়। পাল্টে দেয় রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক চরিত্র। চতুর্থ সংশোধনীর আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান ছিল সংসদীয় পদ্ধতিতে। সংসদ বা প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রবর্তন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘোষণা করা হয় নতুন রাষ্ট্রপতি। কোন ভোট ছাড়াই তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। সংবিধানে বলা হয়, তিনি আজবীন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ন্যায় দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থাৎ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আজীবনের জন্য ক্ষমতা নিজের হাতে নেন শেখ মুজিবুর রহমান।
শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতির হাতে বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ন্যাস্ত করা হয়। যেমন, চতুর্থ সংশোধনীর আগে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের জন্য একটি বিধান ছিল। এতে বলা হয়েছিল, বিচারক অপসারনে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন লাগবে। শেখ মুজিবুর রহমান সেটা পরিবর্তন করে সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নেন। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর এক আদেশেই সুপ্রিমকোর্টের চারজন বিচারপতির চাকুরি খেয়ে ফেলেন। চাকুরিচ্যুত হওয়া ৪ জনের মধ্যে প্রবীনতম আইনজীবী শ্রদ্ধেয় টিএইচ খান এখনো বেঁচে আছেন। আল্লাহ তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন।
মোট কথা, শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই বিচার বিভাগের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিল। বিচারকদের তাঁকে হাতের পুতুল বানানো হয় চতুর্থ সংশোধনীতে। আমরা কিন্তু একথা গুলো বলতে এখন লজ্জা পাই। কারন এটা বললে শেখ মুজিবুর রহমান যদি লজ্জিত হন। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমানকে লজ্জিত করা যাবে নাা! অথবা আমরা বিষয় গুলো সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নই।
এবার আসি কেন এ কাসুন্দি টানলাম। একটা বিষয় বলতে চাচ্ছি। সেটা যাতে সহজে বোধগম্য হয়, এজন্যই পুরাতন কাসুন্দি টানলাম।
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাহাদাৎ বার্ষিকী আজ। খুবই অল্প সময় তিনি পেয়েছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য। অল্প সময় পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন অনেক। মানুষের অদম্য ইচ্ছা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা থাকলে সবই সম্ভব। এটা প্রমান করে গেছেন শহীদ জিয়াউর রহমান। একটি জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। কিভাবে, কারা মুক্ত করেছিলেন সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আরেকদিন সে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। আজকের আলোচনা বিচার বিভাগে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করলেন। শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন বিচার বিভাগ। জিয়াউর রহমান বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে দিলেন। চাইলে তিনি এ ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা করেননি। বিচার বিভাগে কর্মরত বিচারকরা যাতে নির্ভয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারেন, সে ব্যবস্থা করলেন।
বলতে পারে সেটা কেমনে করলেন তিনি?
সুপ্রিমকোর্টের কোন বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে পারে। বিচারকরা এ সমাজেরই মানুষ। তারাও দুর্নীতিতে জড়াতে পারেন। তাই সবকিছুতেই একটা চ্যাক অ্যান্ড ব্যালেন্স লাগে। সুতরাং বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তদন্তের জন্য একটি সংস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। সংবিধানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান করলেন। এই জুডিশিয়াল কাউন্সিল কিভাবে গঠিত হবে সেটাও বলে দিলেন সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে। যে সংশোধনিটি বাতিল করেছিল আওয়ামী বিচারক খায়রুল হক। ৫ম সংশোধনীতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের প্রক্রিয়ায় বলা হয়, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কর্মে প্রবীন অপর দুই বিচারক হবে সদস্য। অর্থাৎ ৩ সদস্যের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে অভিযোগ তদন্তের জন্য। তারা তদন্ত করে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দেবেন। সে অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন।
বিচারক নিয়োগের বিষয়টিও শেখ মুজিবুর রহমান নিজের ইচ্ছার অধিনে নিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান এটাও ফিরিয়ে দিলেন সুপ্রিমকোর্টের হাতে। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ মোতাবেক সুপ্রিমকোর্টে বিচারক নিয়োগের প্রথা চালু করলেন তিনি। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির একক এখতিয়ারে কিছুই রাখলেন না। কোন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যাতে স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারেন, সেটাই ছিল এই প্রক্রিয়া গুলো অনুসরনের মূল কারন। এক ব্যক্তির হাতে সব ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলে সহজেই ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বৈরাচার হয়ে উঠে। জিয়াউর রহমান সব ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে নয়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন।
শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক নেতা থেকে সরকার প্রধান ও নিজে বিনা ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন। তিনি বিচার বিভাগের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জিয়াউর রহমানের পার্থক্যটা এখানেই। জিয়াউর রহমান ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিচার বিভাগের ক্ষমতা নিজের হাতে না রেখে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সুপ্রিমকোর্টের কাছে। কাকে এখন গণতান্ত্রিক এবং কাকে স্বৈরতান্ত্রিক বলবেন, সেটা আপনারাই সিদ্ধান্ত নেন।
এবার আসি আমার আগের আলোচনার ধারাবাহিকতায়। উপরের এটুকু বললাম শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ষ্মরণে।
আগের আলোচনা গুলো যারা পাঠ করেছেন নিশ্চয়ই কত গুলো বিষয় মনে আছে। খায়রুল হক কতৃক তত্ত¦াবধায়ক সরকার বাতিল, রায় লিখতে জালিয়াতি, রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ১০লাখ টাকা গ্রহন এবং প্রাসঙ্গিক অনেক আলোচনা করেছি। নিশ্চয়ই সে গুলো থেকে কিছুটা হলেও পরিস্থিতি জানা গেছে।
২০০০ সাল। শেখ হাসিনার প্রথম প্রধান মন্ত্রিত্ব কালের প্রায় শেষ দিক। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে নিয়োগ নিয়ে পিতার আদর্শ অনুসরণ করলেন। প্রথমবারের মত ৩জনকে সুপারসিড করে নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের আপিল বিভাগে নিয়োগ দিলেন। এনিয়ে প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনার প্রয়োজন মনে করলেন না। যা জিয়াউর রহমানের সময় থেকে একটি প্রথা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সুপ্রিমকোর্টে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করা। এটা ছির একটি প্রতিষ্ঠিত প্রথা। কিন্তু শেখ হাসিনা আপিল বিভাগে নিয়োগ দিলেন একেবারেই নিজের ইচ্ছায়। প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনা ছাড়াই। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান নিজের লেখা-‘তত্ত¡াবধায়ক সরকারের দিন গুলি এবং আমার কথা’ বইয়ে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। এনিয়ে তুমুল আন্দোলনের কথাও আগের আলোচনায় বলেছিলাম। বিচারপতি গোলাম রব্বানী এবং মো: রুহুল আমিনকে আপিল বিভাগে নেয়ার প্রতিবাদে কড়া আন্দোলন হয়েছিল। এতে সুপ্রিমকোর্টের স্বনামধন্য সিনিয়র আইনজীবী এবং সুপ্রিমকোর্ট বারের সাবেক সভাপতি খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ, সুপ্রিমকোর্ট বারের তৎকালিন সভাপতি ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদসহ নবীন-প্রবিন মিলিয়ে ২৫জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দেয়া হল। মাত্র কিছুদিন আগে শেখ হাসিনার সরকার জননিরাপত্তা আইনটি তৈরি করেছে। এ আইনে জামিনের কোন বিধান নেই। অর্থাৎ জননিরাপত্তা আইনে মামলা হলে কোন আদালত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জামিন দিতে পারবে না। অত্যন্ত কঠিন এবং কালো আইন ছিল এটি।
নতুন এ আইনে মামলা হল সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তারা সুপারসিড করে নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। এর আগে চট্র্রগ্রামের একটি হোটেল থেকে ইফার সামগ্রী ছিনতাইয়ের অভিযোগে বিএনপি নেতা মোর্শেদ খানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়। এটাই সম্ভবত জননিরাপত্তা আইনের বড় নেতার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা ছিল।
তিনি হাইকোর্টে আগামী জামিনের জন্য আসলেন। এ আইনে দায়ের করা মামলার আসামী এর আগে কেউ হাইকোর্টেও আসেননি। তৎকালীন বিচারপতি আবু সাঈদ আহমদ ও বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে একটি বেঞ্চ ছিল। আবু সাঈদ আহমদ তখন হাইকোর্ট বিভাগের সিনিয়র বিচারপতিদের অন্যতম। খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিয়োগ পাওয়া। সেদিন মামলাটির শুনানীতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। জননিরাপত্তা আইনে প্রথম কোন রাজনীতিক হাইকোর্টে জামিনের জন্য এসেছেন। অথচ, এ আইনের জামিন চাওয়ারই কোন সুযোগ নেই। কৌতুহল ছিল হাইকোর্ট কি বলে সেটা দেখা। তখন আমি দৈনিক ইনকিলাবে কাজ করি। ইনকিলাব ওই সময় দেশের সবচেয়ে বেশি সাক্যুলেশনের পত্রিকা। টানা দুইদিন এ আবেদন শুনানী হল। ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ ছিলেন মোর্শদ খানের আইনজীবী। রায়ে একটি পদ্ধতি বের করা হল। যেহেতু সরাসরি জামিনের বিধান নেই আইনে। বিচারকদ্বয় একমত হয়ে রায়ে বলে দিলেন, চার্জশীট না হওয়া পর্যন্ত আসামীদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা যাবে না। কেন স্থায়ী জামিন দেয়া হবে না, এমর্মে রুলও জারি করা হল।
এ মামলাটি শুনানী অবস্থায়ই ২৫ আইনজীবীর বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছিল। তারাও একদিন পর একই আদালতে গেলেন। যেহেতু সুপ্রিমকোর্টের মোষ্ট সিনিয়র আইনজীবী এবং বার-এর সাবেক ও বর্তমান সভাপতি মামলার আসামী। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছিল হাইকোর্ট জামিন দিতে দেরি করবে না। আইনজীবীদের সবার জামিন হয়ে গেল পরের দিনই। এই দুই জামিনের সূত্র ধরে জননিরাপত্তা আইনের দায়ের হওয়া মামলার আসামীরা হাইকোর্টে আসতে থাকেন। তখন সারা দেশে প্রচুর মামলা দেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। দলে দলে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীরা আসছেন জামিনের জন্য। সবার বেলায় প্রায় একই আদেশ। চার্জশীট না হওয়া পর্যন্ত গ্রেফতার এবং হয়রানি করা যাবে না। মোটামুটি রিলিফ নিয়েই বাড়ি ফিরছেন সবাই। কারন তখনো সুপ্রিমকোর্টকে পুরোপুরি কব্জায় নেয়া সম্ভব হয়নি শেখ হাসিনার পক্ষে। ক্ষমতায় চার বছরে ৪০ জন বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন। তবে তারা তখনো সিরিয়ালে জুনিয়র। আগের সরকার গুলোর নিয়োগ দেয়া ন্যায় পরায়ন ব্যক্তিরা রয়েছেন তখনো কোর্টে।
এর মাঝেই আবার আইনটি চ্যালেঞ্জ করে রীট আবেদন করা হয়। একজন আইনজীবী এ রীট আবেদনটি করেন। এটাকে কালো আইন হিসাবে আখ্যায়িত করে রীট আবেদনটি করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকরের স্পিরিটের সাথে সাংঘর্ষিক। বিচারপতি এম এ আজিজ ও বিচারপতি শামসুল হুদার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ ছিল তখন। এম এ আজিজ ন্যায় পরায়ণ এবং সাহসি বিচারপতি হিসাবে তখন সুপ্রিমকোর্টে সুপরিচিত। তাঁকে পরবর্তীতে চার দলীয় জোট সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর বিরুদ্ধেই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন করেছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও বামেরা। একটা মাত্র নির্বাচন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেটা ছিল চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। ওই নির্বাচনে চার দলীয় জোট ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ও বিএনপি প্রার্থী বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছিল। তারপরও এম এ আজিজকে সহ্য করেনি আওয়ামী লীগ। তাঁর সাথে বেঞ্চে অপর বিচারক শামসুল হুদা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ প্রাপ্ত। বাড়ি গোপালগঞ্জ। তিনি এক সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। এরশাদ আমলে জাতীয় পার্টিতেও যোগ দিয়েছেন। উপজেলা ইলেকশনও করেছিলেন এরশাদ জামানায়। শেখ হাসিনা তাঁকে বিচারক নিয়োগ করেছিলেন। জননিরাপত্তা আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ মামলায়ও যা হওয়ার তাই হল। বিচারপতি এম এ আজিজ রায় দিলেন জননিরাপত্তা আইন বাতিল করে। এটা অসাংবিধানিক আইন হিসাবে আখ্যায়িত করা হল তাঁর রায়ে। কিন্তু শামসুল হুদা জুনিয়র বিচারক হিসাবে বললেন, তিনি ভিন্নমত পোষণ করে। প্রাকাশ্য আদালতে এম এ আজিজের রায়ের পর তিনি শুধু ভিন্নমত ঘোষণা করলেন। এতে রায়টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। অথাৎ একজন বাতিল করলেন জননিপরাত্তা আইন। আরেকজন বাতিল করলেন না। নিয়ম অনুযায়ী মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে গেল। মোষ্ট সিনিয়র একজনের নেতৃত্বে তৃতীয় বেঞ্চ গঠিত হল। তৃতীয় বেঞ্চে আইনটি অসাংবিধানিক ও অবৈধ বলেই রায় দেয়। অর্থাৎ এম এ আজিজের রায় বহাল থাকে। শামসুল হুদার রায় বাতিল হয়ে যায় তৃতীয় বিচারকের রায়ে। মোট কথা জননিপরাত্তা আইনটি কালো আইন হিসাবেই স্বীকৃতি পেল সুপ্রিমকোর্টে।
এতে স্পষ্ট শেখ হাসিনা প্রথম জামানায়ও ক্ষমতা ধরে রাখতে দমন পীড়ন কম করেননি। তখনো ব্যাপক দমন পীড়ন এবং দলীয়করণ করেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় ফিরতে তাঁর জন্য বড় বাঁধা হয়ে দাড়ায় তত্ত¡াবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। সংবিধানে তখন তত্ত¡াবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল। কোন উপায় নেই। ক্ষমতা ছাড়তে ই হবে। নির্বাচন হবে তত্ত¡াবধায়ক সরকারের অধীনে! তবে ক্ষমতা ছাড়ার আগে প্রশাসন নিজের মত করেই সাজিয়েছিলেন। প্রধান কমিশনার হিসাবে বসিয়েছিলেন গোপালগঞ্জের আবু সাঈদকে। অপর নির্বাচন কমিশনার হিসাবে বসানো হয়েছিল জনতার মঞ্চখ্যাত সাবেক সচিব শফিউর রহমানসহ অনুগত ব্যক্তিদের। প্রধান উপদেষ্টা সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের বাড়িও ছিল গোপালগঞ্জে। তবে তিনি হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হয়েছিলেন এরশাদ জামানায়। আপিল বিভাগে গিয়েছিলেন ১৯৯১ সালের বিএনপি জামনার শেষ দিকে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তাঁকে সিরিয়াল অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি বানিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ অবরসপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। সংবিধান অনুযায়ী তিনি তখন প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন।
২০০১ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার ব্যাপক ভরাডুবি হল। শেখ হাসিনা দেখলেন, সাজানো প্রশাসন এবং নিজের পছন্দের নির্বাচন কমিশন থাকলেও ভোটে জেতা যায় না। ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে প্রয়োজন তত্ত¡াবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় বাতিল করা। এজন্য ২০০১ সালের পর থেকেই তত্ত¡াবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়েও তাঁর নানা আপত্তি ছিল। তিনি এ ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য প্রস্তাবও পেশ করেছিলেন। জরুরী আইনের সুবাদে মঈন-ফখরুদ্দিনের ইন্ডিয়া দালালীর পরিণতি স্বরুপ শেখ হাসিনার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয় ২০০৯ সালে। তখনই শেখ হাসিনা ফন্দি আটেন তত্ত¡াবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কিভাবে বাতিল করা যায়। নিজের হাতে ক্ষমতা রেখে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার পথ খুজেন তিনি। আর সে পথটি সহজ করে দেয় তাঁর শতভাগ অনুগত খায়রুল হক, সুরেন্দ্র কুমার, মোজাম্মেল ও সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। ৭ বিচারপতির মধ্যে এ চারজন তত্ত¡াবধায়ক সরকার বাতিলের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। এই চার পান্ডবের আওয়ামী দালালীর ফল হচ্ছে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া।